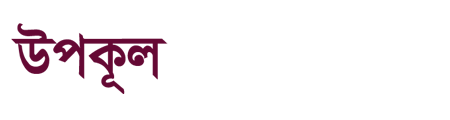[পর্ব-৪: মাদ্রাসা পর্ব]
তখন শীতকাল। ধানক্ষেতে পানি শুকিয়ে গেছে। একবাড়িতে নতুন চালের ভাত রান্না হলে তার ম-ম ঘ্রাণ আরেক বাড়িতে বাতাসের সঙ্গে ঢেউ খেলে খেলে চলে যায়। এমন সময় আবার কাঁধে বাঁক নিয়ে দুধঅলা আসতেন। বাড়ি বাড়ি দুধ দিয়ে যেতেন। দুধ মাপতেন বাঁশের তৈরি এক ধরনের চোঙায়। আমাদের জন্যও এক সের করে দুধ কিনতেন বাবা। তখন কেজি বা লিটার প্রচলন ছিল না। সবই সের হিসেবে চলতো।
তো একদিন সকাল বেলা বাড়ির দরোজায় দাঁড়ানো বাবা। দুধঅলা এলেন। তার পেছনে পেছনে এলেন মোয়া-জিলেপিঅলা। তখন তিন-চার কেজি ধানে এককেজি মোয়া মিলতো। ছয়-সাত কেজি ধানে মিলতো এক কেজি জিলাপি। জিলাপিঅলা সব বাড়িতে যেতেন না। যেতেন কেবল যেসব বাড়িতে ধানমাড়াই হয়, সেসব বাড়িতে। তাও ঠিক ধানমাড়াইয়ের সময়। আর বাড়ির দরোজায় দাঁড়িয়েই হাঁক ছাড়তেন, ‘ও-ই মোলা লইবোনি? মোলা? ও-ওই জিরাপি লইবোনি? জিরাপি?’ সাধারণত বাড়ির ছোটরা ইঁদুরের গর্ত থেকে তুলে আনা জমানো ধান দিয়ে মোয়া-জিলাপি কিনতো। আর খাওয়ার সময় অবশ্যই বাড়িসুদ্ধ সবাই খেতো।
তো সেদিন আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেই মোয়া-জিলাপিঅলা যাচ্ছিলেন, অমনি আমি বললাম, একটা জিরাপি দেন। জিলাপিঅলা বললেন, ধান আছে? জবাবে ‘না’-সূচক মাথা নাড়ালাম। কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। অমনি জিলাপিঅলা একটি জিলাপি হাতে ধরি দিয়ে বললেন, ‘নে খা। ধান দিতে অইবো না।’ আমি হাত বাড়িয়ে নিলাম। খেতে খেতে বাড়িতে ঢুকলাম। বাবা বললেন, ‘যা আজ পুকুর থেকে মাছ ধরুম। তোর দাদির কাছেত্তুন জাল লই আ।’
মাঝেমাঝে ফজরের নামাজের ঈমামতিও আমাকে করতে হয়। ফজরের নামাজের ঈমামতি যে মাঝেমাঝে আমাকে করতে হয়, এই তথ্য গোপন রাখতে হতো মামার নির্দেশে।
জিলাপিটুকুন শেষ করে দুই হাতকে মুষ্ঠিবদ্ধ করলাম। যেভাবে মোটরসাইকেল চালানো হয়, সেভাবে। আর মুখে এক ধরনের ব্রোমমমমমমমমমমমমমমম শব্দ তুলে একদৌড়ে নানাবাড়ি হাজির। নানির সামনে যেতেই বললেন, ‘কিরে কালা? কিল্লাই আইছস?’ আমি কী জন্য এসেছি, হঠাৎ করেই তা ভুলে গেলাম। কিছুক্ষণ দম নিয়ে বললাম, ‘দা-দা-দা-দি, আ-ব্বা-জি ক-ই-ছেন, আন-নে-গো জালখান দিতেনননননননননননন।’ আগেই বলেছি, আমি নানিকে দাদি ডাকতাম। তো নানি আমার তোতলামি দেখে প্রায় বেহুঁশ হওয়ার দশা। চিৎকার করে উঠলেন, ‘ওরে আঁর কালা মানিকের কী অইছেরে? তোতলাই কা রে?’ তার চিৎকারে ছোট খালা, মামা, পাশের বাড়ির মহিলারা এসে জড়ো হলেন। চিৎকার শুনে মা আমার ভোট ভাইকে নিয়ে হাজির। পেছন পেছন বাবাও। সকাল থেকে কী কী ঘটেছে, নানি জানতে চাইলেন। আমি বললাম। বাবাও বললেন। নানি এবার ক্ষেপে গেলেন বাবার ওপর। মেয়ে-জামাতা হলেও নানি আমার বাবাকে ছেলের মতো দেখতেন। আর নাম ধরেই ডাকতেন। তুই সম্বোধন করতেন। (এখানে বলে নেওয়া ভালো, আমাদের গ্রামাঞ্চলে ওই সময়ে মেয়ের জামাইয়ের সামনে সাধারণত শাশুড়িরা যেতেন না। বেড়ার আড়ালে থেকে অমুক পুত বলে সম্বোধন করতেন, আপনি বলতেন। কিন্তু আমার নানি ও আমার বাবার ক্ষেত্রে ছিল ভিন্ন)।
নানি চিৎকার করে বললেন, ‘তুই অনো খাড়াই রইছসনি? যা বড় হুজুররে নিয়ে আয়?’ আমার বাবা কোনো প্রতি উত্তর করলেন না। হনহন করে বেরিয়ে গেলেন। ফিরলেন সেই সন্ধ্যার দিকে। গিয়েছিলেন সাত-আট মাইল দূরে চরবাটা। কোনো এক বড় হুজুরের বাড়িতে। সেখানে সবিস্তারে বলার পর বড় হুজুর একটা তাবিজ দিলেন। সেটি রুপার মাদুলিতে পুরে তাগায় বেঁধে ডান হাতে পরতে হলো আমাকে। সেই মাদুলি সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত আমার হাতে ছিল।
সেই যাই হোক। মূল প্রসঙ্গে আসি। আমার তোতলামির খবর শুনে মক্তবের মৌলবি ইয়াহিয়া হুজুর এলেন। কিছুক্ষণ কথা বলার পর নানিকে বললেন, ‘আমনের নাতিরে হাফেজি পড়ান। তোতলামি চলি যাইবো গই।’ যেই কথা, সেই কাজ। আমার জন্য নতুন একখানা কোরআন শরিফ আনা হলো। নুরানি ছাপা। অর্থাৎ হাফেজরা সাধারণ ছাপানো কোরআন শরিফ পড়েন না। তাদের কোরআন শরিফ হয় অপেক্ষাকৃত ছোট, ছাপাও ছোট। আঁকাবাঁকা হরফ। আমার জন্যও তাই আনা হলো। আমাকে জেবল হক মেম্বারের বাড়ির দরজার মক্তব থেকে নিয়ে ভর্তি করা হলো গুচ্ছগ্রাম ৪ নম্বর কলোনির জামে মসজিদ মক্তবে। পুরো এলাকায় সব মসজিদই বাঁশের বেড়া ও ওপরে নাড়ার ছাউনি। কেবল এই মসজিদটি পূর্ণ পাকা। সেখানে ঈমাম নিজাম হাফেজ। তিনি আমার মায়ের ফুপাতো ভাই। তার কাছে হাফেজি পড়া শুরু। রাতদিন মসজিদেই থাকি। খাই হুজুরের বাড়িতে। রাতে একা ঘুমাই মসজিদে। পাঁচবেলা আজান দেই। মাঝেমাঝে ফজরের নামাজের ঈমামতিও আমাকে করতে হয়। ফজরের নামাজের ঈমামতি যে মাঝেমাঝে আমাকে করতে হয়, এই তথ্য গোপন রাখতে হতো মামার নির্দেশে। কারণ ওই রাতে মামা ছুটি না নিয়েই শ্বশুর বাড়িতে যেতেন। পরদিন জোহরের সময় এসে হাজির হতেন। কমিটি জানতো না কিছু।
ডাংয়ের দৈর্ঘ্য সতের-আঠারো আর গুলির দৈর্ঘ্য ছয়-সাত ইঞ্চি। এই ডাং-গুলি খেলা দুতিন রকমের, আর ছিল নানা কায়দা-কানুন; অবশ্যই তা স্থান-কাল-পাত্রভেদে।
সারাক্ষণ মসজিদে থাকতে থাকতে মনটা বিষয়ে উঠতো। যেদিন হুজুর চরবাটা খাসের হাট যেতেন, সেদিন আমার হাতে স্বর্গ নেমে আসতো। সেদিন আমি যথারীতি মসজিদের আলমারির পেছন থেকে ডাংগুলি-মারবেল-লাটিম বের করে নিয়ে মাঠে চলে যেতাম। টুপি খুলে, পাঞ্জাবি খুলে, লুঙ্গিতে গিঁট দিয়ে ডাংগুলি-হাডুডু কিংবা গোল্লাছুট খেলায় মেতে উঠতাম।
তবে সেবারই ছিল আমার শেষ ডাংগুলি খেলা। হুজুর গেছেন খাসের হাট। আমি আসরের আজান দিলাম। তিন চারজন মুসল্লি এলেন। তাদের ইমামতি করলেন। নামাজ শেষে যে যার মতো চলে গেলেন। মসজিদের পেছনে আমার ফুপুর বাড়ি। আমার বয়সী আমার ফুপাতো ভাই মাহফুজ। সে আমার ডাংগুলি খেলার প্রধান সঙ্গীও। বাড়ির উত্তর পাশে গিয়ে দিলাম ডাক—‘মামমমমমা-হ-ফফফুজ্যা।’ অমনি সে বেরিয়ে এলো।
বললাম, ‘চঅল। ডাংগুলি খেখেখেলি।’ সেও বললো, ‘চল।’
এখানে বলে রাখা ভালো—আমরা যারা বেড়ে উঠেছি অজপাড়াগাঁয়ে, তাদের অনেকেরই শৈশব-কৈশোর কেটেছে প্রথমত রাখালি, দ্বিতীয়ত দিনমজুরি এবং তৃতীয়ত অনিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে। খেলার সঙ্গী ছিল মার্বেল-লাটিম আর ডাং-গুলি। রাজধানী থেকে শুরু করে মফস্বল শহরগুলোয় যখন ক্রিকেট জনপ্রিয় উঠেছিল, তখনও ডাং-গুলি ছিল আমাদের প্রিয় খেলা। মেহেদি গাছের শক্ত ডাল দিয়ে তৈরি হতো সেসব ডাং-গুলি। ডাংয়ের দৈর্ঘ্য সতের-আঠারো আর গুলির দৈর্ঘ্য ছয়-সাত ইঞ্চি। এই ডাং-গুলি খেলা দুতিন রকমের, আর ছিল নানা কায়দা-কানুন; অবশ্যই তা স্থান-কাল-পাত্রভেদে।
ডাং-গুলির যত রকম আছে, এর মধ্যে সবচেয়ে মজার হলো— গোত্তাখেলা। এই লেখা সেই গোত্তা নিয়েই। ক্রিকেটের মতো এই খেলারও রয়েছে দুপক্ষ। একপক্ষ ডাংবাজ, অন্যপক্ষ চেকার। একেক পক্ষে একজন থেকে শুরু করে দশ-বারো জন পর্যন্ত থাকে।
খেলার নিয়ম—খোলামাঠের এক প্রান্তে ছয়-সাত ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের একটি গোত্তা (গর্ত) করতে হয়। গোত্তার দুই প্রান্ত ক্রমাগত ঢালু হয়ে মাঝখানের গভীরতা এক থেকে দেড় ইঞ্চি। গোত্তার মাঝ বরাবর আড়াআড়িভাবে গুলি রাখা হয়। এরপর চেকাররা সুবিধামতো মাঠব্যাপী অবস্থান নেয়। প্রত্যেকের হাতেই থাকে ডাং। ডাংবাজ গোত্তার ভেতর ডাংয়ের মাথা ঢুকিয়ে গুলি ছুড়ে মারে সামনের দিকে। এরপর ডাংটি গোত্তার ওপর রাখে আড়াআড়িভাবে। আর চেকাররা হাতে থাকা ডাং দিয়ে তাকে চেক (আঘাত) মারে। গুলিকে চেকাররা উড়ন্ত অবস্থায় ডাং দিয়ে চেক মারতে পারলে ডাংবাজ আউট। আর যদি চেক মারার আগেই গুলি ভূ-পাতিত হয়, তাহলে চেকাররা গুলিটি গোত্তার দিকে ছুড়ে মারে। গুলি গোত্তার ওপর রাখা ডাং স্পর্শ করলে ডাংবাজ আউট। আর স্পর্শ করতে না পারলে গুলিটি যেখানে পড়ে সেখান থেকে ডাং মেপে-মেপে গুনতে হয়।
তখন রক্তের রং আর সূর্যের লালে আঁকা বিশাল প্রান্তরে আর কিছুই দেখতে পাইনি, শুনতে পাইনি কোনো গানও। কেবল কানের কাছে কে যেন বোল বাজাচ্ছিল—অ্যাঁরি, দোঁরি, তেঁরি, চৌরি, চাম্পা, জেক, জান।
এই গণনারও একটা সুন্দর বোল আছে। বোলটি হলো—অ্যাঁরি, দোঁরি, তেঁরি, চৌরি, চাম্পা, জেক, জান। এভাবে প্রতিবার বোল শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পূর্ণ হয় এক ফুল। আর সাত ফুলে এক লাল। এ বোলের যে অংশে এসে গণনা শেষ হয়, ওই সংখ্যক আঙুল, হাতের তালু, মুষ্টিবদ্ধ হাত, হাতের উল্টোপিঠের ওপর গুলি রেখে ডাং দিয়ে সজোরে আঘাত করা হয়। যতণ-পর্যন্ত ডাংবাজকে আউট করা না-যায় ততণপর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ডাংবাজের কর্মকৌশল ক্রিকেটে ব্যাটসম্যানের, চেকচারীদের দায়িত্ব ফিল্ডারদের মতো।
এখানে একটু বলেই নেই, হাফেজি পড়ার কারণে আমার স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো। কিন্তু যখন স্কুলে যেতাম, তখন স্কুল পালানোয় আমার জুড়ি ছিল না। বাড়ি থেকে বই-স্লেট নিয়ে সময়মতো ঠিকই বের হতাম। কিন্তু প্রতিদিন স্কুলে যাওয়া হতো না। চলে যেতাম স্কুলের কাছাকাছি বেড়ি বাঁধের পাশে। সেখানে জড়ো হতাম সমবয়সী যত স্কুল পালানো দুষ্টের শিরোমনি আর কর্মকান্ত রাখালেরা। কেউ মগ্ন হতাম মার্বেলে, কেউ লাটিমে কেউবা আবার ডাংগুলিতে। আজকের মতো সেকালের শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি ছিল না, ছিল রোববারে।
শুক্রবার স্কুল পালানোর একটা সুবিধা ছিল—অধিকাংশ স্যার তেমন খেয়াল করতেন না কে এলো, আর কে স্কুল কামাই করল। হতো না তেমন রোলকলও। স্যাররা ব্যস্ত হয়ে পড়তেন জুমার নামাজে যাওয়ার জন্য। তখন ‘আমরা সবাই রাজা আমাদের সেই রাজার রাজত্বে।’ কেউ ছুটে যেতাম স্কুলের মাঠে, কেউবা বেড়ি বাঁধে।
তো সেদিন মাহফুজ ও আমি মাঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই এসে হাজির। শৈশবে আধুলি দেখিনি, দেখেছি পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা আর সিকি পয়সার কয়েন। একপয়সার কয়েন তখন যায়-যায়। আমরা সিকি পয়সা দিয়ে টস দিতাম। সেদিন টসে জিতে সিদ্ধান্ত হলো আমি প্রথম ডাংবাজ। খেলা শুরু। সময় গড়ায়, সন্ধ্যা হয় হয়। আমাকে কেউ আউট করতে পারছে না। চেকাররা মহাবিরক্ত।
এদিকে ক্ষুধায় পেট চোঁ-চোঁ করছে। তৃষ্ণায় ফেটে যাচ্ছে বুক। খেলা রেখে যেতেও পারছি না। চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে। কিন্তু খেলার নিয়ম বলে কথা। হাল ছেড়েও দেওয়া যাবে না আউট হওয়ার আগে। তাতে ইজ্জত বাঁচবে না। আমি খুব কান্ত। তাই খুব ধীরে বোল বলতে বলতে দৌঁরিতে এসে থামলাম। দৌঁরির নিয়ম অনুযায়ী বাম হাতের মধ্যমার অগ্রভাগে তর্জনীর নখ ঠেঁসে ধরলাম। গুলিটা রাখলাম আঙুলের ওপর লম্বালম্বি। হাতটা সামান্য নিচের দিকে নামিয়ে-মাত্র আলত করে ওপরের দিকে ছুড়ে দিলাম গুলি। সঙ্গে-সঙ্গে ডাং দিয়ে সজোরে বাড়ি দিতেই গুলিটা ভোঁ-ভোঁ করে উঠে গেলো শূন্যে। সবার চোখ সে দিকে। চেকারদের একজন আমার ফুপাতো ভাই মাহফুজ। গুলিটা তার কাছাকাছি নেমে আসতেই সে সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করলো। যে সংগীতের সুর তুলে গুলি শূন্যে উঠেছিল, তার দ্বিগুণ সুর তুলে ধেয়ে এলো আমার দিকে। তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছিল ডালিম দানার মতো টক-টকে লাল সূর্যটা। আর তার রশ্মি এসে আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই গুলি এসে পড়লো আমার কপালের মাঝখানে। ঝাঁ করে কান বন্ধ হয়ে গেলো, নাকের ভেতর আর জিহ্বায় অনুভব করলাম এক ধরনের লবণাক্ত স্বাদ। তখন রক্তের রং আর সূর্যের লালে আঁকা বিশাল প্রান্তরে আর কিছুই দেখতে পাইনি, শুনতে পাইনি কোনো গানও। কেবল কানের কাছে কে যেন বোল বাজাচ্ছিল—অ্যাঁরি, দোঁরি, তেঁরি, চৌরি, চাম্পা, জেক, জান।
চলবে…