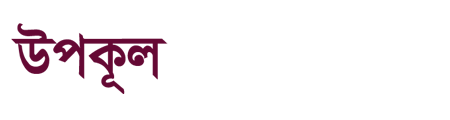[পর্ব-৯: মাদ্রাসা পর্ব]
বেশ ক’দিন হলো মাদ্রাসায় যাই না।
একদিন দুপুরের দিকে হাফেজ নিজাম মামা এসে হাজির। মাকে বললেন, দুপুরের খাবেন। মা তার ছোট ভাইয়ের জন্য রান্না করতে গেলেন। এই ফাঁকে মামা আমাকে বললেন, আর তো মাত্র একপারা। মাদ্রাসায় আয়। তোর বাপ কই? বললাম, চিটাগাং।
কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করলেন, এরপর বললেন, ঠিক আছে। তুই কাল থেকে মাদ্রাসায় আয়। তোর বাপ আমার আগপর্যন্ত বাড়ি থেকে যাওয়া-আসা কর। তোর বাপ ফিরলে জামা-কাপড় নিয়ে মাদ্রায় চলে আসিস। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মামা চলে গেলেন।
আমার মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক কাজ করছে। মাদ্রাসায় পড়তে আর ইচ্ছা করছে না। আবার স্কুলে যেতে চাই। কিন্তু উপায় কী? কাকে বলি কথাটা? কে শুনবে? কাউকে মনের কথা খুলে বলার জন্য পেলাম না। অগত্যা পরদিন থেকে আবার মাদ্রাসায় যাওয়া-আসা শুরু। বাবা বাড়ি ফিরলে একদিন আমি জামাকাপড় দিয়ে মাদ্রাসায় চলে যাই। একমাসের মধ্যেই বাকি একপারাও মুখস্ত। এখন পূর্ণ হাফেজ। কিন্তু নিজাম মামা বলেন, আরও একবার শুরু থেকে পড়ে যেতে হবে। তাতে সময় যত দিনই লাগুক। কথাটা শুনে ভালো লাগলো না।
দেখি সূর্য ধীরে ধীরে মদিনার দিকে নামছে। অনেক দূর থেকে কারও বাঁশির সুর ভেসে আসছে।
সেদিন ছিল সোমবার। চরবাটা ছমির হাটের হাটবার। সবাই গেছে হাটে সপ্তাহের বাজার করতে। মামাও গেছেন সেই সাত মাইল দূরের হাটে। যথারীতি আমার ওপর দায়িত্ব পড়লো আজান দেওয়া-নামাজে ঈমামতি করার। আসরের নামাজের আজানের সময় হলে পুকুরে ওজু করতে বসেছি মাত্র। পেছন থেকে সিনিয়র এক হাফেজ বললেন, কী হাফেজ সাব খবর কী? আমি ওজু থামিয়ে তাকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিয়েই ওজু করতে ঘাটে বসলেন। ওজু শেষে বললাম, হুজুর এই ওয়াক্ত আপনি ঈমামতি করলে ভালো হয়। তিনিও বেশ খুশি হলেন বলে মনে হলো। এখানে বলে রাখা ভালো, নামাজে ঈমামতির ক্ষেত্রে বেশকিছু শর্ত আছে। এর মধ্যে দুটি হলো, অপেক্ষাকৃত বেশি জানাশোনা ও বয়োজ্যেষ্ঠরাই ঈমামতি করবেন। সেই সূত্রে এই সিনিয়রদের অনুরোধ করলে তারা খুশিও হন। হয়তো একারণে এই সিনিয়র হাফেজও খুশি। ওজু শেষে তিনি মসজিদের ভেতরে ঢুকলেন। আমি আজান দিতে দাঁড়ালাম। আজান শেষ হওয়ার আগেই দুই পায়ে ঠক ঠক করে কাঁপুনি শুরু হলো। কোনো রকমে আজান শেষ করলাম। মসজিদে ঢুকতে যাবো, এমন সময় মন বললো, ‘না’। আর না। এবার তুই পালা।
আমি এক পা দুই পা করে মসজিদের মাঠ পার হলাম। এরপর ডানে তাকাই, বামে তাকাই। তাকাই সামনে, তাকাই পেছনে। নাহ! কেউ নেই। বিশাল আকাশের দিকে তাকাই। দেখি সেখানে হালকা মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে। পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাই। দেখি সূর্য ধীরে ধীরে মদিনার দিকে নামছে। অনেক দূর থেকে কারও বাঁশির সুর ভেসে আসছে। আমাদের বাড়ির পাশেই জবিউল্লা নামে একজন জেলখাটা আসামি আছেন। একসময় নৌকায় নাকি মাল্লার কাজ করতেন। কোনো এক বর্ষায় ইলিশ ধরা নিয়ে নৌকায় কাকে যেন খুন করা হয়। সেই খুনের মামলায় নৌকার মাঝিসহ কিশোর জবিউল্লাহরও নাকি জেল হয়ে যায়। সাজা শেষে ফিরে এসে বিকাল বেলায় বাড়ির সামনে বাবলা গাছের নিচে বসেন। দুই হাঁটু মুড়ে বসেন। দরবেশ-ঋষিদের মতো। এরপর বন্ধ করেন দুই চোখ। এরপর এক হাত লম্বা নিতান্তই সাধারণ একটি বাঁশের বাঁশি বের করেন।
আজও সেই গানের সুর। এমন উতলা সুর, মনে হলো এমন সুরে ডুব যে দেয়, তার আর কিছু লাগে না। তার মনে কোনো ভয় থাকে না। সে সব ভয়কে জয় করতে পারে।
টানা মাগরিবের আজান পর্যন্ত সেই বাঁশি বাজান। বাঁশির সুরে গ্রামের মুরব্বিরা বিরক্ত হন। কিন্তু ভয়ে কিছু বলেন না। জেলখাটা আসামি। খুনের আসামি। কী বললে কী করে বসে, জানের মায়া কার না আছে? কিন্তু কিশোর-কিশোরীরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে। তবে, তার কাছে ঘেঁষে না কেউ।
ভয়ে আমরাও যাই না। একদিন মাহফুজ আমাকে জোর করে নিয়ে যায় তার কাছে। লোকটা আমাদের বারো মিঠাই খেতে দেন। আমাকে বলেন, ‘হাফেজি পড়োছ?’ মাথা নাড়ি। তিনি বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। তারপর বলেন, ‘বাঁশি শুনবি?’ আমাদের সম্মতির তোয়াক্কা না করেই কী একটা গানের সুর বাঁশিতে তুললেন, আমরা সব ভুলে তার সামনে বসে থাকলাম। হাটুরেরা আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। তাকাচ্ছে। কেউ কেউ ভর্ৎসনা করছে—বাচ্চা-বাচ্চা পোলাগুলারে জবিউল্লাহ গোমরা করে দিচ্ছে। দেখো আরেকটারে। হানিফ সদাগরের পোলা হকসাব না? ওইটা তো হাফেজি হয় (পড়ে)। ওইটারেও দেখো, ইহুদি-নাসারাগো মতন বাঁশি শোনে! হাটুরেদের কটূক্তিতে আমাদের কিছু এসে-যায় না। আমরা অবশ হয়ে যাই। হারিয়ে ফেলি চলৎশক্তি। কণ্ঠও বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে। কথা বলতে পারি না। মাজারে-মাজারে পীরের সামনে যেভাবে মুরিদ-ভক্ত-আশেকানেরা চোখ বন্ধ করে বসে থাকে, আমরাও সেভাবে থাকি। কখন সন্ধ্যা নেমে আসে বুঝতে পারি না। হঠাৎ আজান ভেসে আসে, টিনের চোঙায় আজান। তখনো আমাদের অঞ্চলে মাইক দেখিনি। উঁচু ঢিবি বা কাঠের মিনারের ওপর উঠে মোয়াজ্জিনরা টিনের চোঙায় আজান দিতেন। তাতে, সিকি মাইল পর্যন্ত সেই আজানের ধ্বনি শোনা যেতো। তো সেদিনও টিনের চোঙায় আজান ভেসে আসতেই জবিউল্লা বাঁশি থামালেন। আমাদের কিছুই বললেন না। খুব ধীর পায়ে হেঁটে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।
আজ মাদ্রাসা থেকে পালিয়ে এসে কোথায় যাবো—ভাবতে না ভাবতেই জবিউল্লাহর বাঁশির সুর শুনে মনটা কেমন উতলা হয়ে উঠলো। আমরা তো মাদ্রাসায় গাইতাম হামদ-নাত। কিন্তু জবিউল্লাহর বাঁশিতে সেই সুর না। অন্য কোনো সুর। কী সুর কী সুর—মনে পড়ে না! হ্যাঁ, মনে পড়ছে, বাবার রেডিওতে শুনেছিলাম একটা গান— ‘প্রাণো সখীরে বাবলা বনের ধারে-ধারে বংশি বাজায় কে?/ বংশি বাজায় কেরে সখী, বংশী বাজায় কে?/ আমার মাথার বেণী খুইলা দেবো তারে আইনা দে।’ আজও সেই গানের সুর। এমন উতলা সুর, মনে হলো এমন সুরে ডুব যে দেয়, তার আর কিছু লাগে না। তার মনে কোনো ভয় থাকে না। সে সব ভয়কে জয় করতে পারে।
তাই নদীর চড়া হেঁটে যেতে হবে অনেক দূর। চড়া ফেলে ডানে বামে গেলেই বিপদ। চোরাবালিতে দেবে যেতে পারে।
আস্তে আস্তে জবিউল্লার কাছে গিয়ে বসি। তার চোখ বন্ধ। গায়ে গেঞ্জি। পরনে ধুতি। গ্রামে সাধারণত লুঙ্গি পরে সবাই। কিন্তু জবিউল্লাহ পরেন না। তিনি ধুতি পরেন। মাঝেমাঝে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি পরেন। শীতকাল এলে বাঁশির পাশাপাশি হাতে থাকে উলের মাফলার। অর্ধেক। তিনি মাফলার বোনেন। বুনে বুনে একে দেন, ওকে দেন। লাল-নীল-সবুজ-হলুদ বিচিত্র রঙের সুতা কিনে আনেন। তারপর হাঁটতে হাঁটতে মাফলার বোনেন, বসে বসে বোনেন।
এখন বর্ষার আগ মুহূর্ত। সেইসব নেই। কেবল বাঁশি আছে। তার পাশে বসে গান শুনতে মাগরিবের আজান পড়ে গেলো। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। আমাদের বাড়ির দূরত্ব মাত্র দশ মিনিটের। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে সোজা ঘর দেখা যায়। ঘরে কেরোসিনের চেরাগ জ্বলে উঠেছে। এখান থেকেই টিমে টিমে আলো দেখা যাচ্ছে। মায়ের জন্য, বাবার জন্য, ভাইয়ের জন্য বুকটা খাঁ-খাঁ করে উঠছে। কিন্তু বাড়ি যাবো না। গেলে আবার মাদ্রাসায় দিয়ে আসবেন বাবা।
আজ যারা সকালে ছমিরহাটে গিয়েছিলেন, তারা বিকালে বাড়ির পথ ধরেছেন। তাদের মধ্যে নদীর পূর্বপারের চরলক্ষ্মীর লোকজনই বেশি। তারা আমাদের বাড়ি থেকে কিছুটা পথ পূর্ব দিকে হেঁটে গেলেই নদী পাবেন। এখন জোয়ার নেই। নদীতে পানি কম। তাই নদীর চড়া হেঁটে যেতে হবে অনেক দূর। চড়া ফেলে ডানে বামে গেলেই বিপদ। চোরাবালিতে দেবে যেতে পারে।
একবার মা-নানির সঙ্গে বড় খালাদের বাড়ি যাচ্ছিলাম। নদীর চড়ায় নামামাত্রই নানি নদীর একটুকরো মাটি আমার মুখে পুরে দিলেন। বললেন, ‘খা। নতুন জায়গায় গেলে মাটিকে সম্মান করতে অয়।’ আমি কোনো প্রশ্ন না করেই সেই মাটিটুকু মুখে দেই। তীব্র লবণাক্ত। তবু গিলে ফেলি। আজ হাঁটুরেদের সঙ্গে যাচ্ছি। কাউকে চিনি না। সবাই অপরিচিত। তারা সবাই বড় বড়। আমার বয়সী কাউকে দেখলাম না। দুই বুড়োর মধ্যে কথোকথন চলছে। একজন বলছেন, ‘এই পোলাগা কাররে? আন্নে চিনেননি?’ অন্যজন বলেন, ‘না’।
আমিও তার বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে ডুকরে উঠলাম। আর তখন মনে হলো—মায়ের বুকে ফিরে এসেছি। আমাকে আর মাদ্রাসায় কেউ নিয়ে যেতে পারবে না!
তারা দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়েন। একজন বলেন, ‘তুই কার পোলারে?’ আমি চুপ। আরেকজনের প্রশ্ন—‘কোনবাইত যাইবি?’ আমি চুপ। এবার একজন গর্জে ওঠেন—‘কথা কছ না ক্যা?’ এবার আমি ভয়ে কেঁদে ফেলি। কাদার ভেতর আমার হাঁটুপর্যন্ত দেবে যায়। আমি নড়তে পারি না। নদীর পানির অংশ এখনো অনেক দূর। আমার লুঙ্গি কাদায় একাকার। পাঞ্জাবির কোণাও ডুবে গেছে। কাঁদতে দেখে সবচেয়ে বয়স্ক লোকটি গলার স্বর নরম করে বললেন, ‘তুঁই কার পোলা, কার নাতি—না কইলে ক্যামনে চিনুম। আর যাইবা কই? বাই কই?’ এবার তোতলাতে থাকি। কিছু বলতে পারি না। লোকটি কাছে আসেন। এসে আমাকে টেনে তোলেন। বলেন, ‘এবার আঁডো (হাঁটো) আঙ্গো লগে।’ হাঁটতে থাকি। বুড়োটি আবারও বলেন, ‘কোন বাইত যাইবা? তুঁই কার পোলা-কার নাতি?’
বুড়ো লোকটিকে কেমন যেমন আপন আপন লাগে। এবার বলি, ‘আঁই হানিফ সদারের পুত। হাফেজি পড়ি। মাদ্রাসা ছুটি দিছে। অন বেরাইতে যামু খালাগো বাইত। আমিন মোল্লাগো বাইত।’ এখানে বলে রাখি, কদিন আগে আমার মেজ খালার বিয়ে হয়েছে নদীর ওপারে। আমিন মোল্লার বড় ছেলের সঙ্গে। ওই বাড়িকে সবাই একনামে চেনে। বুড়ো আমার কথা শুনে, একগাল হেসে ওঠেন। বলেন, ‘ওরে চোরা! আগে কইবি তো! তুই আমিন মোল্লারে চিনসনি?’ বলি, ‘না দেখি ন কোনোদিন। আগে একদিন গেছিলাম। ওইদিন হেতেনরে (তাকে) দেখি ন। আম্নের মতো বয়স অইবো। হেতেন আঁর খালার হোর (শ্বশুর)। তোই বাই (বাড়ি) চিনুম।’
এবার বুড়ো আমার বাম হাত তার মুঠোয় শক্ত করে ধরেন। বলেন, ‘আরে শালা, আঁইয়ে না আমিন মোল্লা। তোর নানা। আগে কইবি না?’ আমিন মোল্লার কথা শুনে তার সঙ্গী এবার হেঁসে উঠলেন। বললেন, ‘যাক ভালাই অইলো। দরিয়ার মাঝখানে নানা-নাতির হরিচয় অইলো। যান, যান, নাতিরে লই বাইত যান।’ কিছুক্ষণ থেমে আবার বলেন, ‘আম্নের নাতি হেতার বাপ-মারে কই আছেনি?’ আমিন মোল্লা কিছু বলার আগেই বলি, ‘অ্যাঁ।’
আমরা আমিন মোল্লার বাড়ি পৌঁছাতে পৌঁছাতে এশার আজান পড়ে গেলো। ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আমিন মোল্লা আমার খালাকে ডাকলেন। খালার নাম ধরে নয়। নিচের ছেলের নাম ধরে—‘আব্দুল্লার বউ কইগো? দেখো কারে আইনছি!’ খালা লম্বা ঘোমটা টেনে কেরোসিনের চেরাগ হাতে বেরিয়ে এলেন। চেরাগ ঘরের দাওয়ায় রেখে আমার কাছে এলেন। দুই হাতে আমার মুখ তুলে ধরলেন—‘ওরে আঁর বোইনহুতে না রে্।’ বুকের ভেতর শক্ত করে ধরেই হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন খালা! আমিও তার বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে ডুকরে উঠলাম। আর তখন মনে হলো—মায়ের বুকে ফিরে এসেছি। আমাকে আর মাদ্রাসায় কেউ নিয়ে যেতে পারবে না!
চলবে…
জীবনের যতিচিহ্নগুলো-৮