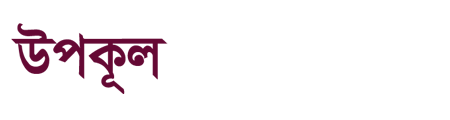(পর্ব-১: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দিনগুলো)
১৯৮৯ সাল। এরশাদের শাসন আমলের শেষের দিকে। আমাদের গ্রামের বাড়ি গুচ্ছগ্রাম। পড়তাম বাংলাবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। টেনেটুনে সব বিষয়ে পাস করে পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছি। কিন্তু এই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু কেন?
কেন?—তার কারণ বলার আগে একটু গুচ্ছগ্রামের বর্ণনা দিয়ে নেই। সম্ভবত আমার বয়স আর এই এলাকার বয়স প্রায় কাছাকাছি। খুব ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। যেটুকু মনে পড়ে, বলি। তখন আমাদের বাড়ি বলতে একটি পুকুর। একটি ঘর। ঘরের পেছনে পূর্বদিকে পুকুর। পুকুর ও ঘরের মাঝখানে পাড়। পাড়ের ওপর চওড়া একখানা তক্তা। সেই তক্তার ওপর ভোরে এসে বসতাম। দুপুর ঘনিয়ে আসার আগে নদীতে জোয়ার আসতো। জোয়ারের পানি আমার পা ভিজিয়ে দিতো। আমি সেই পানি পা নাড়াতাম। কখনো কখনো ছোট ছোট কাঁকড়া আমার সারা পায়ে জড়িয়ে যেতো। আমি চিৎকার করে কাঁদতাম। দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে পড়তাম। মা-বাবার জামাকাপড়ের আড়ালে মুখ লুকাতাম। আমার কান্না কেউ শুনতো না। কেউ দেখতোও না।
আবার বের হতাম। দখিনা বাতাস শোঁ শোঁ করে বয়ে যেতো আমার কানের লতির নিচ দিয়ে উত্তরের দিকে। কেন যেতো সেদিকে? মনে মনে প্রশ্ন করতাম, প্রতিদিন বাতাস এভাবে উত্তর দিকে কেন যায়? উত্তর দিকে আমার নানার বাড়ি। আমি নানিকে শৈশবে দাদি ডাকতাম। আমার জন্মের পর দাদা-দাদিকে দেখিনি। আমার বাবার শৈশবেই তারা স্বর্গবাসী হয়েছিলেন। তাই হয়তো নানিকেই দাদি ডাকতাম। মাঝেমাঝে একা লাগলে সেই দাদিকে ডাকতাম। মনে হতো বাতাসের কাছে যদি বলি, বাতাস হয়তো গিয়ে দাদিকে বলবে। বাতাস যখন আমার কানের কাছে শো-শো আওয়াজ তুলে চলে যেতো, আমিও সুরে সুরে মিলিয়ে ডাকতাম, ‘ও দাদি-ই-ই-ই-ই।’ দাদি শুনতেন কি না জানি না। কিন্তু আমার মনে হতো শুনতেন। তার কিছুক্ষণ পরই দাদি আমার কোচা ভরা পেয়ারা নিয়ে হাজির হতেন। বলতেন নে খা। খেয়ে আঁরে (আমাকে) উদ্ধার কর। আমি এক কামড়ে কিছুটা খেয়ে বাকিটা রেখে দিতাম। বলতাম, আমি যাবো। দাদি কপট রাগ দেখিয়ে বলতেন, কই যাবি? বলতাম, আমনেগো বাইত।
কিছুক্ষণ পর দাদি আমাকে কোলে নিয়ে বের হতেন। শীতের দিনে নাড়া-ভেঙে হাঁটতেন, বর্ষায় ঢেউ ঢেউ জলরাশিতে ঝপঝপ পা ফেলে এগিয়ে যেতেন। মাঝেমাঝে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছতেন। কেন? আজও জানি না। মাঝে মাঝে বলতেন, ‘আঁই মইরলে কবর দিতে আইবিনি? তোরে তো মরার সময় চোখেও দেইখতাননো।’ আমি চুপ থাকতাম। কী বলবো বুঝতাম না। হতভম্ব হয়ে যেতাম। একসময় কেঁদে ফেলতাম।
নানির বাড়িতে চাঁদনি রাতে উঠোনে সবাই গোল হয়ে বসতো। বিশেষত ফাল্গুন-চৈত্র মাসে। ধান মাড়াইয়ের সময়। ঘরের ছাউনি বদলের সময়। অনেক রাত পর্যন্ত রূপকথার গল্প বলতেন নানি ও নানির বয়সী নারীরা। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। কখনো রাক্ষসপুরী থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধারের গল্প বলতেন। কখনো রাক্ষসীর পেটে লালকমলের চলে যাওয়ার গল্প। সেই সব গল্প শুনতাম। মনে মনে নিজেকেও লালকমল ভাবতাম। নিজের অস্তিত্ব নিয়ে শিহরে উঠতাম। কেঁপে কেঁপে উঠতাম। আবার শুরু হতো বড়দের গল্প। সিন্দাবাদ। হাতেম তায়ী। ছয়ফুল মুলুক ও বদিউজ্জামান। মামা আমার একজনই। নানির চার মেয়ে। একছেলে। মামা পঞ্চম শ্রেণী পাস। সুর করে পুঁথি পড়তেন। গাজীকালু-চম্পাবতির পুঁথি। ছহিজঙ্গনামা। বাবা পড়তেন বিষাদসিন্ধু। জলে চোখ ভিজে যেতো। আজগরের ছেলের জন্য কেঁদে কেঁদে সারারাত বুক ভাসাতাম। পরদিন সবই ভুলে যেতাম।
আমরা দুজনে সেই দুটি বাছুরকে ঘোড়া বানাতাম। চড়ে বসতাম পিঠে। অশ্বারোহী পেয়ে বাছুরগুলো যেন বাতাসের বেগে ছুটতো। তিন বাড়ি ঘুরে এসে আবার বাড়ির পাশে গোয়াল ঘরের পাশেই দাঁড়াতো।
ভোর হলে ছোটখালা রোকেয়ার সঙ্গে বের হতাম। নদীর তীরে। ছাট খুঁজতে। আর লরকা মাছ। ছাট—একধরনের ক্ষুদ্র প্রাণী। মেরুদণ্ডহীন। শামুকপ্রজাতির হয়তো। তবে, শামুকের মতো শক্ত খোলস নেই। পুরোটাই মাংস। হাসের প্রিয় খাবার। খলুই ভরে আনতাম। হাসগুলোর খাওয়া দেখতাম। আর লরকা মাছগুলো রান্না হতো। তেল ভাসতো ঝোলের ওপর দিয়ে। সেই তেল গরম ভাতের সঙ্গে মেখে দাদি আমাকে খাওয়াতেন। তার ছোট মেয়েকেও খাওয়াতেন।
বর্ষা এলে আরেক দৃশ্য। চারদিকে জল থই থই। অনেক দূর দিয়ে হাটুরেরা হেঁটে গেলেও ঘর থেকে শোনা যায়। জলে ঝুপঝুপ শব্দ করে। অনেক রাতে কেউ গান ধরে। নানা চিৎকার করে ডাক দেন, ‘ওই-ই-ই-ই কন রে?’ ওই রে, ধ্বনি বাতাসে ও জলের তরঙ্গে ঢেউ খেলে খেলে ভেসে ভেসে যায় রে রে রে রে। এক অদ্ভূত সুর। বাতাসও তাতে তাল দেয়। তাতে ওই রে একসময় হারিয়ে যায়। ফিরতি আওয়াজ আসে। একই ভঙ্গিতে। একই সুরে—‘আঁই জেবল হক গো, মামা আ-আ-আ-আ-আ।’ নানা আমার প্রতিউত্তর শোনেন। কখনো পাল্টা প্রশ্ন করেন, কখনো চুপ থাকেন। কিন্তু আমার কানের কাছে ক্রমাগত বাজতে থাকে, ওই-ই্-ই-ই-উ। আ-আ-আ-আ।
তারপর ভোর হয়ে আসে। দরোজা খুলে ঘরের দাওয়ায় বসি। পূর্বদিকে তাকায়। দেখি লাল টকেটকে বিশাল একখানা থানা নদীর ভেতর থেকে আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠছে, তার ভোরের প্রায়ান্ধকার ভাবও কেটে যাচ্ছে। লাল ঘনঘনে থালাকে আড়াল করে মাঝেমাঝে কার যেন সাম্পানও ভেসে যায়। নাওয়ের বাদামে সে কী বাতাসের আলোড়ন। বাতাস তাকে ঠেলে নিয়ে যায় উত্তরে, একসময় আর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। রোদের ঝলকে আর তাকাতে পারি না। আস্তে আস্তে নামি উঠোনে। উঠোন পার হয়ে বাড়ি কাঁদি। কাঁদি পার হলে নদীর কিনার শুরু। সেখানে ছোট ছোট কাঁকটা, আর ওঁটা (মোটা ঘাসেরর্ ছোট ছোট স্তূপ) ভেসে আসে। জড়ো হয়ে আছে। আরে সমুদ্রের ফেনা। ওঁটার সঙ্গে সমুদ্রফেনার সে কি আলিঙ্গন। যেন তারা সহদর-সহদরা।
তুলে আনি সেই ওঁটা। রোদে শুকিয়ে খটখটে করে নেই। তাতে মা-নানির রান্নার লাকড়ির জোগান হয়ে যায়। আমাদের সঙ্গে যোগ জাফর। সে আমার শৈশবের খেলার সঙ্গী। স্কুলে যেতো না। মক্তবেও না। আমি স্কুলে যেতাম। মক্তবেও। তবু তার সঙ্গে আমার আড্ডাটা বেশি হতো। তাদের দুটি গাভী ছিল। আর ছিল দুটি বাছুর। বাছুরগুলো বেশ বড়। আমরা দুজনে সেই দুটি বাছুরকে ঘোড়া বানাতাম। চড়ে বসতাম পিঠে। অশ্বারোহী পেয়ে বাছুরগুলো যেন বাতাসের বেগে ছুটতো। তিন বাড়ি ঘুরে এসে আবার বাড়ির পাশে গোয়াল ঘরের পাশেই দাঁড়াতো। আমরাও দিগ্বিজয়ী বীরের মতো, নামতাম। তখনো টেলিভিশন দেখিনি। তবে ঘরে তিন ব্যান্ডের রেডিও বাজতো। মা-খালারা শেফালি ঘোষ, কল্যাণী ঘোষের গান শুনতেন। বাবা-মা শুনতেন মোহাম্মদ হাশেম ও শাহ বাঙালির গান।
দুই.
আশ্বিনের শেষাশেষি। মক্তব ছুটি হয়ে গেছে। একটু আগে বৃষ্টি থেমেছে। তাই রাস্তা ভেজা। এছাড়া এই পথে লোকজন কম চলাচল করে বলে রাস্তার একপাশে শ্যাওলা জমে আছে। আমরা সেই শ্যাওলার ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলাকে রকেটের গতির মতো ভাবি। অনেক দূর থেকে দৌড়ি এসে শরীরকে নির্ভার করে দৌড় থামিয়ে দেই, কিন্তু আমরা থামি না। আমাদের দৌড়ের গতি স্কেলেটরের মতো আমাদের অনেকদূর পর্যন্ত নিয়ে যায়। কিন্তু এই নেওয়ার পথে পায়ের ঘর্ষণে দুই দিকে সমানে ময়লা পানি-কাদা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দুই পাশে যারা থাকে, তাদের জামাকাপড় নষ্ট হয়ে যায়। এতে অনেকে বিরক্ত হন। বকা দেন। কেউ কেউ দেন চড় থাপ্পড়ও। তো সেদিনও এমনটি ঘটেছিল।
তার সঙ্গে শেষ দিকে মসজিদের কবরস্থানে। সবাই তাকে কাফনের কাপড় মুখখানা দেখেছে। আমি দেখিনি। আমার সাহস হয়নি।
আমার মক্তব-স্কুলের সহপাঠী আমির হোসেন। মক্তব ছুটির পর যথারীতি আমরা রাস্তায়। আজ সে সবার আগে দৌড় দিয়ে হঠাৎ থেমে অনেকদূর যাওয়ার খেলায় মেতে উঠেছে। আমি পাশে পাশে দৌড়াচ্ছি। হঠাৎই তার পায়ের কাদা এসে লাগলো আমার চোখেমুখে। আমিও দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি। আমার বাম হাত যত দূর সম্ভব ওপরে তুলে কষে একথাপ্পড় বসিয়ে দেই তার কানের ওপর। আমার সেই অতর্তিক থাপ্পড়ে আমির হোসেন হতভম্ব। কিছুই বললো না। না চিৎকার করে কাঁদলোও না। কেবল দুই চোখের কোণা বেয়ে নেমে এলো ক্ষীণ লোনা পানির ধারা। যেই ধারায় মানুষের আস্তজীবনকে বদলে দেয় নুহের প্লাবনের মতো। তাৎক্ষণিক বুঝতে পারিনি। বুঝেছি কদিন পর।
বেশ কদিন পর খেয়াল করলাম, আমির হোসেন মক্তবে আসে না। স্কুলেও না। কার কাছে যেন কার কাছে যেন খবর পেলাম, তার প্রচণ্ড জ্বর। তার বাবাও ডাক্তার ছিলেন। তিনি চিকিৎসা করেছেন সাধ্যমতো। কিন্তু জ্বর সারেনি। এরপর বাংলাবাজারের সবচেয়ে বড় ডাক্তার কিরণ চন্দ্র রায় সাত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে দেখে এসেছেন। এসে কিছু ওষুধ দিয়েছেন, বলেছেন, বড় ধরনের জটিল জ্বর। অন্য রোগও হতে পারে। সুস্থ হওয়া না-হওয়া ওপরঅলার ইচ্ছা। তবে আঘাতটা সরাসরি মস্তিষ্কে লেগেছে।
কিরণ ডাক্তারকে আমার ছোট ফুপু ভাই ডেকেছিলেন। তিনি আমাদের পারিবারিক ডাক্তারও। শুধু পারিবারিক ডাক্তারই নন। আত্মীয়ও যেন। আরেক ডাক্তার বঙ্কিম চন্দ্র রায় তো আমাকে দেখলেই বলতেন, কী রে কিরণ ডাক্তারের পোলা কেমন আছস? পড়াশোনা চলছে তো? নাকি খালি দুষ্টুমি? আদাব দিয়ে বলতাম, জি বাবু চলছে।
তো যেদিন শুনলাম আমিরের জ্বর, ভালো হয় কি না, সন্দেহ, সেদিনই গ্রামের এক বড় আপুর হাত ধরে দেখতে গিয়েছিলাম তাকে। তার মাথার কাছে বসেছিলাম। সে কেবল আমার হাতখানা বুকের ভেতর চেপে ধরে রেখেছিল। তার দুই চোখ বেয়ে ঝরতেছিল অঝরধারায় শ্রাবণধারা। আমিও ধরে রাখতে পারিনি চোখের পানি। কতবার ভেবেছি ক্ষমা চাইবো, কিন্তু ক্ষমা চাওয়া হলো না। উল্টো আমির বললো, বন্ধু, তুই আমার সবচেয়ে বড়বন্ধু, আমার ভাই। তোর কি মনে পড়ে আমরা কেনো দিন একলা কোনো লজেন্স খেয়েছি? আমি তোকে না দিয়ে খেয়েছি? তুই কি আমাকে না দিয়ে খেয়েছিস? গাছের পেয়ারা তোকে না দিয়ে আমি খেয়েছি? নাকি তুই খেয়েছিস? আমার মুখ দেয় কথা বের হচ্ছিল না। আমি শুধু ঠোঁট কামড়ে ধরে ‘না’সূচক মাথা নেড়ে গেলাম। একসময় আমি বললো, একটা কথা বলি, আমি মনে হয় বাঁচবো না। তোরে অনুরোধ করি, জীবনে কারও গায়ে হাত তুলিস না। তোর হাত খুব খারাপ। অলক্ষ্মী। তোর হাত যার গায়ে ওঠে সে মরে যায়। কদিন আগে তুই রাগ করে গরুর বাচুরকে থাপ্পড় দিয়েছিস, সেই বাচুর তার তিন দিনের মাথায় মরে গেছে রে… আমির কথা শেষ করতে পারে না। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। আমিও কাঁদি। সেদিন বুকভাঙা বেদনা নিয়ে ফিরে আসি বাড়িতে। পরদিন ভোর না হতেই শুনি আমির আর নেই। তাকে শেষ দেখা দেখি মসজিদের কবরস্থানে। সবাই কাপনের কাপড় সরিয়ে মুখখানা দেখেছে। আমি দেখিনি। সাহস হয়নি।
চলবে…